গত ৫ই মার্চ ২০২১ সালে রাষ্ট্রচিন্তার আমন্ত্রণে ‘গণতন্ত্র ও জনবাদ’ বিষয়ে অনলাইন বক্তৃতা দেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও নৃবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে দুনিয়াব্যাপী অন্যতম প্রধান একজন ইতিহাসবিদ ও তাত্ত্বিক হিশেবে বিবেচিত। বাংলাদেশেও লেখক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষার্থী, ইতিহাসবিদদের কাছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় অতি পরিচিত নাম।
পার্থ চট্টোপাধ্যায় আশির দশকে শুরু হওয়া সাড়া জাগানো নিম্নবর্গের ইতিহাস অধ্যয়ন গ্রুপের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কে অবস্থিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান এবং মিডল ইস্টার্ন, সাউথ এশিয়ান ও আফ্রিকান স্টাডিজের সিনিয়র রিসার্চ স্কলার হিশেবে কর্মরত আছেন। এছাড়াও তিনি ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত কলকাতায় অবস্থিত সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স–এর ডিরেক্টর এর দায়িত্বেও নিয়োজিত ছিলেন।
পলিটিকাল সোসাইটি, সিভিল সোসাইটি, সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র, আধুনিকতা, জাতীয়তাবাদ, উত্তর–ঔপনিবেশিক সমাজ সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সর্বমহলে বিবেচিত। সাম্প্রতিককালে তিনি বিশ শতকে অবিভক্ত বাংলার জন–ইতিহাস নিয়ে কাজ করছেন।
দুনিয়াব্যাপী গণতন্ত্রের ক্রম অবনতি ও নতুন ধরনের স্বৈরতান্ত্রিকতার উত্থানের কালে ‘পপুলিজম’ তথা ‘জনবাদ’ বহুল চর্চিত রাজনৈতিক পরিভাষা। আমরা মনে করি, অধিকতর ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক সমাজ–সম্পর্কের জন্য যারা লড়াইরত, তাদের এ বিষয়ে সম্যক বোঝাপড়া থাকা জরুরি।
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার শ্রুতিলিখন তৈরি করেছেন রেজওয়ানুর রহমান পান্থ ও সারোয়ার তুষার। অরাজ নেটওয়ার্কের অনুরোধে পরবর্তী পরিমার্জন–এর মাধ্যমে শ্রুতিলিখনটিকে বর্তমান ভার্সনে উপনীত করে দিয়েছেন খোদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রাষ্ট্রচিন্তা, পার্থ চট্টোপাধ্যায়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অরাজ কৃতজ্ঞ।–সম্পাদক]

রাষ্ট্রচিন্তার পক্ষ থেকে যে আপনারা আমায় বলার সুযোগ দিয়েছেন তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। আমি যতদূর জানি আপনারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাজনীতি সংক্রান্ত নানারকম তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করে থাকেন আপনাদের এই ফেসবুক সিরিজটাতে। আপনাদের সারোয়ার তুষার যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, ভাবলাম সাম্প্রতিক যে বিষয় নিয়ে শুধু আমাদের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলেই নয়, সারা পৃথিবীতেই যা নিয়ে যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে এবং সেটা শুধু পণ্ডিত মহলেই নয়, সাধারণ সংবাদপত্র, টেলিভিশনের আলোচনায় এবং সাধারণ রাজনীতির আলোচনাতেও যাকে বলা হচ্ছে পপুলিজম বা জনবাদ, তাই নিয়ে বলব। জনবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কী, এই বিষয়টা নিয়ে আমি সাম্প্রতিককালে কিছু চিন্তাভাবনা করেছিলাম, তাই নিয়ে কিছু লেখালেখিও করেছি। আমার মনে হলো যে সেই বিষয়ে হয়তো আপনাদের কাছে যদি আমি আমার ভাবনা খানিকটা ব্যক্ত করি তাহলে হয়তো আপনাদের তার থেকে খানিকটা আলোচনার খোরাক জুটতে পারে। সেই হিসেবে আমি আপনাদের এই বিষয়টা নিয়ে কিছু বলছি। তারপরে আমি নিশ্চয়ই আশা করবো আপনারা আপনাদের প্রশ্ন তুলবেন এবং তাই নিয়ে খানিকটা আলোচনা হবে।
গণতন্ত্র ও জনবাদ। আমি ‘গণতন্ত্র’ দিয়েই শুরু করি। গণতন্ত্র ব্যাপারটা কী, আমার ধারণা আমরা মোটামুটি সকলেই তার সঙ্গে খানিকটা পরিচিত! কারণ এটা এখন সম্প্রতিকালে, অন্তত আমাদের যুগে এই ধারণাটা ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে গেছে। সব দেশে গণতন্ত্র নেই। কিন্তু যে দেশে নেই, সেখানেও গণতন্ত্র হওয়া উচিত— এইরকম বক্তব্য শোনা যায়। আপনারা জানেন, এই যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার। বার্মাতে যে ঘটনা ঘটে চলেছে এখন–সাংঘাতিক। সেখানেও আমরা দৈনিক দেখতে পাচ্ছি সেখানকার মানুষ কীভাবে সেনাবাহিনীর একটা জঘন্য অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়েও তারা গণতন্ত্রের জন্য লড়ছে, বলছে গণতন্ত্রের জন্য আমরা প্রাণ দিতে রাজি আছি। এইরকম একটা ঘটনা যেখানে আমাদের চোখের সামনে ঘটতে পারে, সেখানে এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই উঠবে যে, এই ধারণাটা এত শক্তিশালী হলো কী করে? এবং এই ধারণাটার পিছনে এমন কী ব্যাপার আছে যাতে এত মানুষকে এরকমভাবে সেটা নাড়া দিতে পারে। আমি প্রথমে সেখান থেকেই শুরু করি।
আপনারা যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পলিটিকাল সায়েন্স খানিকটা চর্চা করেছেন, তারা সকলেই জানবেন যে এই গণতন্ত্রের বিষয়ে যখন পশ্চিমের যারা তাত্ত্বিক, তারা যখন লিখতে শুরু করেন বা এই বিষয়ে বলতে শুরু করেন, প্রথমেই তারা চলে যান প্রাচীন গ্রিসে। প্রাচীন গ্রিস। সেখানেই এই ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্রের ধারণার জন্ম হয়েছিলো। এটাই হচ্ছে প্রচলিত ইতিহাস। সে ইতিহাসে এমনিতে ভুল কিছু নেই, কিন্তু কতগুলো বিষয় নিয়ে আমাদের একটু খেয়াল রাখা উচিত। যদিও প্রাচীন গ্রিসে এবং তার পরবর্তীকালে রোমের সাম্রাজ্যে গণতন্ত্র বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দেখা দিয়েছিলো বটে, কিন্তু সাধারণভাবে তখনকার পণ্ডিত সমাজে এবং যারা শাসন করতেন, সেই শাসকগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে কিন্তু গণতন্ত্র সম্বন্ধে খুব একটা ভালো ধারণা ছিলো না।
গ্রিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই, যেমন প্লেটো, মোটেই গণতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন না। সাধারণভাবে গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের মত ছিলো, এটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের রাজত্ব, যেসব মানুষরা স্বভাবতই কোনো উচ্চ সংস্কৃতির বিষয়ে অবহিত নন, তারা হয়তো কৃষক কিংবা কারিগর এই জাতীয় লোক। তারা যখন রাজত্ব করার মতো অবস্থায় চলে আসে, সেই রাজত্ব মোটেই কোনো ভালো রাজত্ব হতে পারে না। এটাই সাধারণভাবে মত ছিলো। এদের মধ্যে একমাত্র যিনি বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল, তাঁর যে ‘পলিটিকস’ নামের বই, তাতে তিনি বিভিন্ন রকমের রাজ্য শাসনব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, সেসব বর্ণনার মধ্যে উনি গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসির কথা বলছেন। একটা মোটামুটি মন্দের ভালো হিসেবে ডেমোক্রেসিকে উনি সম্পূর্ণ বাদ দেননি। মন্দের ভালো এই ডেমোক্রেসির মধ্যে বেশ কিছু ভালো দিক উনি বলেছেন।

একটা বিষয় কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার যে, এই প্রাচীন গ্রিসই বলুন অথবা রোমই বলুন, সেখানে যখন ‘সাধারণ মানুষ’ বলা হচ্ছে তার মানে কিন্তু এই নয় যে এখনকার গণতন্ত্র বলতে আমরা যেভাবে বুঝি অবাধ ভোটাধিকার, অর্থাৎ আপামর জনসাধারণ স্ত্রী–পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই রাজ্যশাসনের বিষয়ে একটা মতামত দেবে এবং সেই মতামত অনুসারে রাজ্য শাসিত হবে— এই যে ধারণা এখন আমরা গণতন্ত্র বলতে যেটা বুঝি, সেটা কিন্তু গ্রিস বা রোমে ছিলো না৷ কারণ আমরা অনেকসময় ভুলে যাই যে গ্রিস বা রোমের সমাজে কিন্তু একটা বড় অংশ ছিলো যারা আসলে কৃতদাস, স্লেইভ। স্বভাবতই কোনোরকম রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করার প্রশ্নই উঠতো না। তারা তাদের মালিকের অধীনে কাজ করতো। তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের কোনো প্রশ্নই আসতে পারতো না। দ্বিতীয়ত, ‘সাধারণ মানুষ’ বলতে এখানে পুরুষ মানুষই বোঝানো হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই কিন্তু প্রাচীন এই সমাজে মহিলাদের রাজনীতি বা রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার কোনো অবকাশ ছিলো না। সুতরাং এই অর্থে প্রাচীন গ্রিসে ডেমোক্রেসি বলতে গেলে, হ্যাঁ, ধারণার দিক থেকে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকেরা এই ধারণাটাকেই মান্য করেন। এর যে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, সেই পরিপ্রেক্ষিত যে এখনকার অবস্থার সঙ্গে মেলে না সেটা অবশ্যই তারা স্বীকার করবেন। ফলে এইটা মনে রাখা উচিত যে, ডেমোক্রেসির ধারণা, অথবা একটু পরেই আমি যে বিষয়টা তুলবো republicanism বা রিপাবলিকের ধারণা, যাকে আমরা বাংলায় বলি প্রজাতন্ত্র, সেই ধারণাও রোমে ছিলো। সেটাও কিন্তু ওইরকম আপামর জনসাধারণের রাজ্যশাসন নয়। গণতন্ত্র সম্বন্ধে পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে যে ধারণাটা গুরুত্বপূর্ণ, যেটা বিশেষ করে আমাদের এই এশিয়ার যে অংশটা আমরা যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলাম, সেই ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আমরা অনেকটাই গ্রহণ করেছি, এখনো আমরা অনেকটাই ব্রিটিশ ধরনের রাজ্যশাসন ব্যবস্থার মধ্যে আছি।
এই ব্রিটিশ গণতন্ত্র ব্যবস্থার যেটা মূল ধারণা, সেটা বোঝাতে কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ডেমোক্রেসি কথাটা অত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো না। তখন বলা হতো representative government অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যাদের প্রতিনিধি বলে বেছে দেবেন ভোট দিয়ে, সেই প্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের হয়ে রাজ্য শাসন করবেন। এটা হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, যেটা বিলেতের পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা হিসেবে আমরা জানি। কিছুদিন বাদে বাদে, অর্থাৎ সাধারণভাবে বিলেতের হিসাব অনুযায়ী পাঁচ বছর বাদে বাদে, একটি করে সাধারণ নির্বাচন হবে এবং সেই সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টের যারা সদস্য নির্বাচিত হবেন, সেই পার্লামেন্ট সদস্যরা একটা মন্ত্রীসভা তৈরি করবেন। প্রধানমন্ত্রী ঠিক হবে এবং সেই মন্ত্রীসভা দেশ শাসন করবে। এইটাই হচ্ছে গিয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা। এটাকে representative government বলা হচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কিন্তু ডেমোক্রেসির সঙ্গে এটাকে স্পষ্টভাবে মেলানো হতো না। তার কারণ আছে। লিবারেল বা উদারনৈতিক তাত্ত্বিকদের মতে এই প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ গভর্নমেন্ট। অনেকেই আপনারা পড়েছেন হয়তো জন স্টুয়ার্ট মিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তার একটা বই–ই আছে রেপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে। তাতে উনি স্পষ্ট ব্যাখা করে বুঝাচ্ছেন কেন প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাই অন্য সব ব্যবস্থার তুলনায় শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা। জনগণের নির্বাচিত সরকারের ধারণাটা কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপদ্ধতির একেবারে কেন্দ্রস্থলে আছে।
‘জনগণ’ বলতে কিন্তু এটা মনে রাখা উচিত যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা আমরা এত শুনে থাকি, সেখানে কিন্তু অবাধ ভোটাধিকার ছিলো না। বহুদিন পর্যন্ত, ধরুন যাদের শ্রমিক শ্রেণি বলা হয়, বিলেতে তাদের ভোট এসেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। ব্রিটেনে মেয়েদের ভোট, অবাধ ভোটাধিকার হয়েছে বোধ হয় ১৯২৩ বা ১৯২৪ সালে। তার আগে পর্যন্ত মহিলাদের ভোট ছিলো না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরেকটা জিনিস আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আমরা ভুলি না নিশ্চয়ই। সেখানে যদিও সম্পত্তি বা শিক্ষা বা ট্যাক্স দেওয়া অনুযায়ী ভোটাধিকারের যে নিয়মগুলো ছিলো, সেগুলো অনেকদিন আগেই উঠে যায়, কিন্তু মেয়েদের ভোট ১৯২০’র দশকে এসেছে। এবং যারা প্রাক্তন কৃতদাস আফ্রিকান অর্থাৎ আফ্রিকান–আমেরিকান জনগোষ্ঠী তাদের ভোটাধিকার হয়েছে ১৯৬০’র দশকে, সিভিল রাইটস যখন স্বীকৃত হলো তারপরেই তাদের সাধারণভাবে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। তার আগে পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্টেটে কিন্তু অধিকাংশ আফ্রিকান–আমেরিকানদের ভোট ছিলো না। সুতরাং এগুলো সবই গণতন্ত্রের প্রাক–ইতিহাস বলতে পারা যায়।

এইজন্য বলছি যে, আমাদের একটা জিনিস প্রথমেই ভালোভাবে বুঝে রাখা প্রয়োজন যে আমরা এখন গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি, অর্থাৎ আপামর জনসাধারণ তথা স্ত্রী–পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যে ভোটাধিকার এবং সেই ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকারের যে শাসন, সেই ধারণাটা কিন্তু অত্যন্ত আধুনিক ধারণা। এর প্রাক–ইতিহাস থাকতেই পারে কিন্তু এই ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে। এখানে গণতন্ত্র সম্বন্ধে আরেকটা সাধারণ কথা, এটা আপনারা অনেকেই শুনে থাকবেন, অনেকসময়ই এটা বলা হয়। আব্রাহাম লিংকনের সেই বিখ্যাত কথা, ডেমোক্রেসি হচ্ছে ‘গভর্নমেন্ট অফ দ্যা পিপল, বাই দ্যা পিপল, ফর দ্যা পিপল’। এই যে তিনটা ধারণা, এই তিনটা ধারণা আমি একটু বিশদভাবে বলি।
‘গভর্নমেন্ট অফ দ্যা পিপল’ বলতে বোঝায় এমন শাসনব্যবস্থা যা জনগণই প্রতিষ্ঠা করেছে। জনগণ প্রতিষ্ঠা করেছে বলতে কী বোঝায়? এই ধারণাটা বুঝতে হলে কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যেগুলোকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয়ে থাকে, ডেমোক্রেটিক রেভ্যুলিউশন, সেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরমধ্যে স্বভাবতই ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের কথা আসে। ফরাসি বিপ্লব নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ আপনারা জানেন যে ফরাসি বিপ্লবে একটা রাজতন্ত্র, একটা অত্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের অবসান হলো একটা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পর যেটা প্রতিষ্ঠিত হলো, সেই প্রথম কন্সটিটিউশন হলো রাইটস অফ মেন এন্ড সিটিজেন। অর্থাৎ নাগরিক অধিকার এবং মানবাধিকার; এই দুটো ধারণা। নাগরিক অধিকার, সিটিজেনস রাইটস আর মানবাধিকার, রাইটস অফ মেন। সেটা অবশ্য তখনো শুধু মেনই বলা হয়েছে। এই দুটো ধারণার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিলো রাজতন্ত্রের অবসান এবং প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা। এই গোটাটা মিলিয়ে যে ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেটা হল জনগণের সার্বভৌমত্ব। sovereignty অর্থাৎ people’s sovereignty; এই People’s sovereignty বা জনগণের সার্বভৌমত্ব ধারণাটা যে গণতন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে গেলো, এটা আধুনিক গণতন্ত্রের একেবারে কেন্দ্রস্থলে এখনো রয়েছে। আপনি ফ্রান্সের কথাই ভাবুন, বিপ্লবের পর যেটা প্রতিষ্ঠিত হলো, অথবা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র যুদ্ধ, যেটা আমেরিকান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বলা হয়। তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যারা ইউরোপীয় সেটলার, সেখানে যারা কলোনি স্থাপন করেছে, তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল। এখানেও আবার মনে রাখতে হবে, এই যে সেটলার যারা, যারা জনগণ, তার মধ্যে কিন্তু আমেরিকার যারা আদি–অধিবাসী অর্থাৎ নেটিভ আমেরিকান, তারা কিন্তু এর অংশীদার নন। তারা এই রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বাইরে। বহুদিন পর্যন্ত, অতি সম্প্রতিকাল পর্যন্ত নেটিভ আমেরিকানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তার সম্পূর্ণ বাইরে ছিলো। তাদের রিজার্ভেশন বলে আলাদা জায়গা দেওয়া হয়েছিলো। সেখানে তাদের থাকতে হতো একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে। এখন সম্প্রতিকালে খুব সামান্য অল্প অল্প করে তাদের কিছুকিছু প্রতিনিধি মার্কিন রাজনীতিতে দেখতে পাওয়া যায়। বহুদিন পর্যন্ত এদের কোনো স্থানই ছিলো না। সুতরাং আমেরিকার ‘জনগণ’ বলতে কিন্তু ইউরোপ থেকে আসা যে সেটলার, যারা উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সেই সেটলারদের কথাই বলা হচ্ছে। তারাই আমেরিকান ‘পিপল’। কিন্তু তারা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের যে ঔপনিবেশিক শাসন তার অবসান ঘটিয়ে নিজেদের রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করলো।
ফ্রান্স আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে দক্ষিণ আমেরিকায় বেশ কয়টা নতুন রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয় যাদের বলিভারের বিপ্লব বলা হয়, সায়মন বলিভারের বিপ্লব। এরা সবই স্পেনের যে সাম্রাজ্য ছিলো তার বিরুদ্ধে ঠিক একই রকম ইউরোপীয় সেটলারদের বিদ্রোহ। স্পেনের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে নিজেদের আলাদা আলাদা রিপাবলিক তৈরি করল, যেমন পেরু, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা। এইগুলা সবই কিন্তু রিপাবলিক, সবগুলোই তথাকথিত জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এরা যে জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তার প্রমাণ হলো এরা প্রত্যেকেই একটি করে সংবিধান, কনস্টিটিউশন তৈরি করল। সেই কনস্টিটিউশনই হচ্ছে নতুন শাসনব্যবস্থার ভিত্তি, তার সাংবিধানিক দলিল। সেই প্রত্যেকটি সংবিধানের গোড়াতেই একটি কথা লেখা থাকে— আমরা এদেশের জনগণ, আমরা এই সংবিধান রচনা করে এক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলাম। এটাই হচ্ছে প্রতিটা সংবিধানের প্রতিজ্ঞাপত্র। এটাই হলো গভর্নমেন্ট অব দ্যা পিপল অর্থাৎ জনগণই যে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করলো, তার ঘোষণা। এটাই হলো জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রমাণ, তার দলিল।

এই দলিলগুলোতে সাধারণভাবে যে দুটো কথা বলা হয়— সাধারণ ভোটাধিকার এবং প্রজাতন্ত্র— ইউরোপের অনেকগুলো দেশে কিন্তু, এই যেরকম ব্রিটেনের কথা বললাম, এইভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, রাজতন্ত্র রেখেই এক ধরনের representative government আনা হয়েছে। এই কারণে আমি বলছিলাম যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে ডেমোক্রেসি কথাটা সরাসরি ব্যবহার করা হতো না, কারণ ডেমক্রেসি কথাটার মধ্যে ওই ফরাসি বিপ্লবের একটা গন্ধ রয়ে গেছে এবং অনেকদিন পর্যন্ত ব্রিটেনে ওই ফরাসি বিপ্লবের ছোঁয়াটা যাতে না লাগে সেইজন্যে রিপাবলিকান কথাটাও সেইভাবে ব্যবহার করা হতো না। যদিও তার আগের যুগে ব্রিটেনেও প্রচুর রিপাবলিকান ধারণার কথা উঠেছে কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে ওই পুরো ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ উদারনীতি, উদারনৈতিক মত তথা লিবারেলিজম, তাতে ডেমোক্রেসি কথাটা খুব শুনতে পাওয়া যায় না, রিপাবলিক কথাটাও খুব শুনতে পাওয়া যায় না। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, অর্থাৎ মানুষের ভোটাধিকার দিয়ে যে পার্লামেন্ট তৈরি হবে সেই পার্লামেন্ট কিন্তু রাজা বা রানির পদটা রেখেই পার্লামেন্টের শাসন। এইভাবেই রাজতন্ত্র সত্ত্বেও এক ধরনের গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে এই গণতন্ত্র আরও অনেক ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপের অনেক দেশেই এই অবস্থা হয়েছে। সুতরাং এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ দ্যা পিপল–এর দ্বিতীয় পথ যা প্রজাতন্ত্র নয়।
‘ফর দ্যা পিপল’— এইটা আরেকটু বিশদভাবে বলতে হবে এখন। আগেই বলে নিই, ‘বাই দ্যা পিপল’ অর্থাৎ জনগণ নিজেই নিজেকে শাসন করছে, এটা কিন্তু আমার মতে পৃথিবীর কোথাও হয়নি, আজ অব্দি হয়নি। অর্থাৎ যে অর্থে বলা যেতে পারতো ‘গভর্নমেন্ট বাই দ্যা পিপল’, এটা কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রে বা আধুনিক কোনো রাষ্ট্রে, অর্থাৎ যেখানে কোটি কোটি লোকের বাস, সেই রকম জনবহুল কোনো রাষ্ট্রে কিন্তু এটা বলতে পারা যাবে না যে ‘গভর্নমেন্ট বাই দ্যা পিপল’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ সবসময়ই ‘পিপল’ এবং তার শাসক যারা তাদের মধ্যবর্তী অনেকগুলো স্তর থাকবে। সেখানেই প্রতিনিধির ধারণাটা আসছে। জনপ্রতিনিধি কে এবং প্রতিনিধি কীভাবে বাছা হবে? সেই প্রতিনিধির ক্ষমতা কতদূর? সেই প্রতিনিধিকে কখন সরানো যাবে? তার বদলে আর কাকে বসানো যাবে? এই প্রশ্নগুলো স্বভাবতই গণতন্ত্রের আলোচনাতে সবসময়ই আসছে। কিন্তু জনগণ নিজেই নিজেকে শাসন করছে এই ধারণাটার কিন্তু কোথাও প্রাতিষ্ঠানিক নিদর্শন পাওয়া যাবে না। গণতন্ত্রের এই বিষয়ে অত্যন্ত ভালো আলোচনা পাওয়া যায় ফরাসি বিপ্লবের ঠিক আগের যুগে এবং ফরাসি বিপ্লবের সমসাময়িক সময়ে।
যেমন রুশোর মত ছিলো যে, একটি আইন যখন পাশ হবে, সেটা সব মানুষ একসঙ্গে আলোচনা করে তারপরে ভোট দিয়ে সেই আইন পাশ করবে না কেন? অর্থাৎ শুধু পার্লামেন্টের যারা সদস্য তারাই শুধু আলোচনা করে একটা আইন তৈরি করবে কেন? তাতে সমস্ত মানুষ, ব্যাপক জনসাধারণ অংশ নেবে না কেন? এখন এখানে সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা সবসময় ওঠে যে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে একটা আলোচনায় কী করে আনা যাবে এবং তাতে কী করে একটা আইনের যে খুঁটিনাটি জটিলতা সবসময় থাকবে, সেটা কী করে ওইরকম একটা সর্বসাধারণের মধ্যে আলোচনার পর স্থির হতে পারে? রুশোর প্রশ্নের উত্তরে সবাই এখন বলেন, এটা হতে পারে না। সর্বসাধারণ বড়জোর একটা মোটাদাগের নীতি বলে দিতে পারে। কিন্তু সেই নীতি একটা আইন ব্যবস্থার মধ্যে রূপায়ণ করা, এটা স্পেশালিস্টদের কাজ অর্থাৎ যারা এই বিষয়ে বিজ্ঞ লোক, অভিজ্ঞ লোক এরকম মানুষই এ কাজটা করতে পারে। সুতরাং জনগণের এটাই কর্তব্য যে সেই ধরনের মানুষ যেন তারা প্রতিনিধি হিসেবে বাছতে পারে, নির্বাচন করতে পারে। তাহলেই গণতন্ত্রের কাজটা ঠিকমতো হতে পারে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের একটা বক্তব্য সেখানে থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সবসময় সক্রিয়ভাবে প্রশাসন চালাচ্ছে বা আইন প্রণয়ন করছে, এটা হওয়া সম্ভব নয়। যদিও এই ধরনের প্রচেষ্টা কিন্তু বিভিন্ন সময়ে হয়ে এসেছে এবং এখনো হয়ে থাকে। আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়তো জানবেন যে, চীনে যখন কালচারাল রেভ্যুলিউশন তথা সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়েছিলো, তখনো এই ধরনের চেষ্টা হয়েছিলো যে, সমস্ত সরকারি সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, সাধারণ জনসভা ডেকে সেইখানে নেওয়া হবে। কিন্তু এটা আমরা জানি যে এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা অন্তত সাম্প্রতিককালে, এবং ভবিষ্যতেও যেটুকু দেখতে পাওয়া যায়, কোনো বড় রাষ্ট্রে এইরকম ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কোথাও নেওয়া যায়নি। নেওয়া সম্ভব বলেও অনেকে মনে করেন না। অর্থাৎ ‘গভর্নমেন্ট বাই দ্যা পিপল’ ধারণাটা কিন্তু বাস্তবে কার্যকর হয়নি বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। আমার মতে সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।
‘গভর্নমেন্ট ফর দ্যা পিপল’ এটাই আরেকটু বিশদভাবে বলতে হয়। ‘গভমেন্ট ফর দ্যা পিপল’ অর্থে সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য, তাদের সুবিধার জন্য, তাদের দাবি মেটানোর জন্য নিয়োজিত যে সরকার বা শাসনব্যবস্থা সেটাই হলো গভর্নমেন্ট ফর দ্যা পিপল। এইখানেই পপুলিজমের ধারণাটা সম্প্রতিকালে বিশেষ করে উঠেছে। কারণ পপুলিজম তথা জনবাদ বলতে যে সমস্ত নেতা বা দলের কথা বলা হয়, তারা সকলেই জোর গলায় বলেন যে, এখন যারা শাসন করছেন তারা একটা এলিট সম্প্রদায়। তারা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেন না। সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়ার প্রতি তারা মোটেই সেদিকে নজর দেন না। বরং ক্ষুদ্রগোষ্ঠী যারা ইতোমধ্যেই ধনী, বিত্তশালী, সম্পত্তিবান, তাদের কথাই তারা ভাবে। যারা পপুলিস্ট বা জনবাদী নেতা/নেত্রী বা জনবাদী দল, তারা সকলেই বলে যে, যে প্রশাসন বা সরকার বা শাসনব্যবস্থা আছে তা আরও বেশি করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষের অভাব–অনটন মেটানোর কথা তাদের ভাবা উচিত। এটাই হবে যথার্থ গণতন্ত্র। অর্থাৎ তারা অনেক বেশি করে ‘গভর্নমেন্ট ফর দ্যা পিপল’, এই দিকটাতেই জোর দিয়ে থাকেন।

এখন এই বিষয়টাও খানিকটা প্রাক–ইতিহাস আছে। আমি দুদিক থেকে এই আলোচনাটা করতে চাই। এক হচ্ছে পশ্চিমের দেশ, যেহেতু এখন পশ্চিমেই এই পপুলিজমের কথাটা খুব বেশি করে শোনা যাচ্ছে এবং এই নিয়ে অনেক বেশি করে লেখালেখি কথাবার্তা হচ্ছে। সুতরাং সে কথাটা খানিকটা আলোচনা করতে হবে। আর অন্যদিকে আমাদের মতো দেশে, এশিয়া আফ্রিকা অঞ্চলে যে পপুলিজম, সেই কথাটাও আমি আলাদা করে আলোচনা করবো কারণ আমার মতে এই দুই অঞ্চলের জনবাদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যটা আমাদের খেয়াল রাখা উচিত।
পশ্চিমের জনবাদের কথাটাই প্রথমে বলি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন জায়গায় এই পপুলিস্ট কথাটা উঠেছিলো। আপনারা যারা একটু ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তারা হয়তো জানবেন যে রাশিয়ান পপুলিজম সম্বন্ধে একসময় অনেকরকম কথা হয়েছিলো। তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি আছেন। নারোদনিক বলা হতো তাদের। যেরকম তলস্তয় যিনি বিখ্যাত লেখক, তাঁর মতকে অনেকে মনে করেন অনেকটাই নারোদনিক ধারণার কাছাকাছি। কিন্তু নারোদনিকদের সঙ্গে তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপের যারা মার্কসবাদী তাদের অনেক রকম যোগাযোগ ছিলো, বিরোধিতাও ছিলো। নারোদনিকদের রাশিয়ান পপুলিস্ট বলা হতো। এদের মূল ধারণা ছিলো যে, রাশিয়াতে সেইসময় যারা অভিজাত শ্রেণি এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তারা তখন ভয়ানকভাবে পশ্চিম ইউরোপের দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দিতো, পশ্চিমের শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি অনুকরণ করার চেষ্টা করতো। তাদের ওয়েস্টার্নাইজার বলা হয়। তার বিরুদ্ধে একটা মত, এবং এই মতটা অনেকটাই কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির অল্পবয়েসী ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে খুব বেশি করে দেখা গিয়েছিলো যে ‘গ্রামে চলো’। প্যারিসে বা জার্মানিতে গিয়ে লেখাপড়া শেখা–এটা রাশিয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কারণ আসল রাশিয়া আছে গ্রামে, রাশিয়ার কৃষকদের মধ্যে চলে যাও। কৃষক সমাজের কীভাবে উন্নতি হবে সেই দিকটা ভাবো। এক ধরনের স্যোসালিজমের কথাও তারা বলতেন যে স্যোসালিজমটা কিন্তু ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণির যে স্যোসালিজম, তার মতো নয়। অর্থাৎ কলকারখানায় কাজ করে যে শহরের মজুর, তাদের শ্রেণি–সংগঠন, তাদের ট্রেড ইউনিয়ন, তার মাধ্যমে একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে, এই যে ধারণাটা তখন পশ্চিম ইউরোপে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, নারোদনিকদের বক্তব্য ছিলো যে রাশিয়ার পক্ষে সে পথটা মোটেই উপযুক্ত নয়। কারণ রাশিয়াতে সেইরকমভাবে শিল্প তৈরি হয়নি, শিল্পশ্রমিক বলতে কিছু নেই। সুতরাং গ্রামে কী হবে সেইটাই তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়। স্বতন্ত্র গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক ধরনের সমাজতন্ত্র হতে পারে, এই বিশ্বাসটাই তাদের পপুলিজম। অনেকে মনে করেন যে আমাদের ভারতবর্ষে গান্ধীবাদ এক ধরনের পপুলিজম, বিশেষ করে খানিকটা হয়তো এই কারণে যে গান্ধী খুব মন দিয়ে তলস্তয় পড়েছিলেন এবং খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন তলস্তয়ের লেখা থেকে। এই যে গান্ধীর সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে যে কথাটা চালু হলো, বিশেষ করে শহরের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে, যে শহরে থেকে রাজনীতি করা একটা শৌখিন রাজনীতি, আসল রাজনীতি করতে হলে গ্রামে যেতে হবে, কৃষকদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে হবে। এটাও এক ধরনের পপুলিজম বলে অনেকে বলেছেন। অনেকের হয়তো বাংলাদেশের মওলানা ভাসানীর কথা মনে হতে পারে। যাই হোক, এগুলো সবই কিন্তু আধুনিক বা সমসাময়িক যে পপুলিজম তার খানিকটা প্রাক–ইতিহাস বলা যায়।
সম্প্রতি ইউরোপে যে পপুলিজমের কথাটা আসছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতট কিন্তু এই: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে যে সমাজব্যবস্থা তৈরি হয়েছিলো তার মধ্যে থেকে এই পপুলিজমের জন্ম। সেই ইতিহাসটা একটু দেখতে হয়। সেই ইতিহাসটা এরকম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপে ওয়েলফেয়ার স্টেট অর্থাৎ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মূল কথা হচ্ছে যে কেবলমাত্র ভোটের অধিকার নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যে প্রয়োজন তার একটা বড় অংশ মেটানোর দায় সরকারকে নিতে হবে। এই দায় যে সরকার নিলো ওয়েলফেয়ার স্টেটের মাধ্যমে, তার ফলে প্রত্যেক মানুষের জীবিকার দায়িত্ব, সেই জীবিকা কোনো কারণে যদি তার না থাকে, তার যদি কোনো কাজ না থাকে, বেকার হয়ে যায়, তাহলে তার ন্যূনতম ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার নেবে। অর্থাৎ ইউরোপের সব দেশে প্রবর্তিত হলো বেকার ভাতা৷ এই বেকার ভাতা প্রত্যেক বেকার মানুষের প্রাপ্য। তারপর স্বাস্থ্য। বৃটেনসহ পশ্চিম ইউরোপের সব দেশে এক ধরনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস চালু হলো, অর্থাৎ সরকারি হাসপাতালে সমস্ত রকম চিকিৎসা বিনা খরচায় প্রত্যেক নাগরিকের প্রাপ্য। এরপর ধরুন শিক্ষা। সমস্ত স্কুল শিক্ষা বিনা বেতনে হবে। অনেক দেশে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির শিক্ষাও মোটামুটি বিনা বেতনে বা নামমাত্র বেতনে পাওয়া যেত। বাসস্থান একটা বড় জিনিস। সরকারি খরচে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হল। খুব সামান্য ভাড়ায়, অনেকক্ষেত্রে এক ধরনের লিজের মারফত, কিছুদিন বাদে সেই বাড়ির মালিকানা সাধারণ মানুষ পাবে। এই যে ব্যবস্থাগুলো, অর্থাৎ ওয়েলফেয়ার স্টেটের মূলকথা ছিলো, এই সুবিধাগুলো দেওয়া হচ্ছে সমস্ত জনগণের নাগরিক অধিকার হিসেবে। এখানে কিন্তু কারোর বিশেষ প্রয়োজন আছে কি নেই— এ প্রশ্ন উঠছে না। যে কেউ, যে কোনো নাগরিক চাইলেই এই সুবিধাগুলো পেতে পারে। এই জনকল্যাণমূলক ওয়েলফেয়ার স্টেট পশ্চিম ইউরোপের সবগুলো দেশেই ১৯৫০’র দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।
১৯৭০ থেকে শুরু করে ওয়েলফেয়ার স্টেটের ব্যবস্থা সম্পর্কে নানারকম সমালোচনা উঠতে লাগলো। সমালোচনার মূলকথা হচ্ছে যে এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে, এরজন্য সরকারকে ভয়ঙ্কর বেশি ট্যাক্স (কর) আদায় করতে হচ্ছে এবং তার ফলে বিশেষ করে যাদের উপার্জন বেশি তাদেরকে প্রচণ্ড বেশি হারে কর দিতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা ওঠে যে, এতে প্রচুর অপচয় হয়। যাদের সামর্থ্য আছে, যাদের ব্যক্তিগত উপার্জন বেশি, যাদের ধনসম্পত্তি আছে, যারা ব্যক্তিগতভাবে এই খরচটা মেটাতে পারেন, যেমন ধরুন প্রাইভেট হাসপাতালের খরচ বহন করতে পারেন, অথবা ধরুন ইউনিভার্সিটির পড়াশোনার খরচ মেটাতে পারেন। তারাও কিন্তু সরকারি সুযোগ নিয়ে বিনা খরচে হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছেন, বিনা খরচে তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা কলেজ–ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। এটা কেন হবে?
এই যে সমালোচনাগুলো শুরু হলো তার থেকেই সত্তরের দশক থেকে ব্রিটেনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে অর্থনীতিবিদ এবং বিভিন্ন পলিসি বিষয়ে যারা আলোচনা করেন, তাদের প্রচারে এই কথাটা বেশি করে শুরু হলো যে ওয়েলফেয়ার স্টেট ব্যবস্থাটা আর চালানো উচিত নয়। ওয়েলফেয়ার স্টেটকে সংকোচন করে নিয়ে আসা হোক। রাষ্ট্রকে জনকল্যাণের জায়গা থেকে সরে আসতে হবে। সেই সব পরিসেবা বাজারের হাতে তুলে দিতে হবে। বাজারের মাধ্যমে সত্যি সত্যি যাদের প্রয়োজন তাদের আলাদা করে সনাক্ত করা সম্ভব। যাদের পক্ষে বাজার থেকে নিজের সামর্থ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় অথবা যারা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন না অথবা যাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে পারবে না তাদের সেই সামর্থ্য নেই বলে, শুধু তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করে সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। সেটা রাষ্ট্র করবে। কিন্তু সাধারণভাবে সমস্ত নাগরিকের জন্য এই সমস্ত সুবিধাগুলো খুলে দেওয়া আর চলতে পারে না। এই যে রাষ্ট্র বা সরকারকে এইসব জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম থেকে সরে আসার ব্যবস্থা করা হলো, তাকে বলা হয় নিও–লিবারেলিজম বা নিও–লিবারেল মতবাদ। এই মতবাদ কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে ১৯৮০’র দশকের মধ্যে প্রায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো। এবং ওয়েলফেয়ার স্টেট মোটামুটিভাবে সব জায়গাতেই অনেকটা করে কমে এলো, অনেক জায়গায় প্রায় উঠেই গেলো বলতে পারা যায়।
নিও–লিবেরাল ব্যবস্থার বিরূদ্ধে আবার নব্বইয়ের দশক থেকে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নানারকম ক্ষোভ জমা হতে থাকে। এই বিক্ষোভ সবচেয়ে বেশি করে প্রকাশ পেল ২০০৮–’০৯–এর ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস থেকে। ফিনান্সিয়াল বাজারে হঠাৎ করে প্রায় সমস্ত কিছু হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার মতো যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিলো, সেই অবস্থার পরে, ২০১০–’১১–’১২ এই সময়ে অনেক বেশি করে এইসব দেশে ব্যাপকভাবে যে ধনী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তফাৎটা, ইনইকুয়ালিটি, অসাম্য— এই অসাম্য যে প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে, এটা একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে সকলকে দেখিয়ে দেওয়া হলো। এইখান থেকেই জনগণের প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। এই বিক্ষোভ দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী— দু’রকমই দেখতে পাওয়া যায়। আমি পশ্চিমের কথাটাই বলছিলাম এতক্ষণ, সেখানে এই ধরনের বিক্ষোভ দেখ দিলো। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা যদি বলেন, “অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট”, একরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তৈরি হয়েছিলো। মূল বক্তব্য ছিলো, আমরা হচ্ছি দেশের ৯৯ ভাগ, আমাদের কিছুই নেই, আর দেশের এক ভাগ, শতকরা এক ভাগ মানুষ, তারা সমস্ত সম্পত্তি দখল করে বসে আছে। এই অসাম্য কেন চলবে? এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
অন্যদিকে যাকে আবার দক্ষিণপন্থী বলা যায়, তার একটা বড় উদাহরণ সে সময় ছিলো, “টি পার্টি মুভমেন্ট”। এই টি পার্টি মুভমেন্ট— এরা দক্ষিণপন্থী, কিন্তু এরাও সাধারণ মানুষ। এরা ওই অর্থে ধনী মানুষদের সংগঠন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এরা অপেক্ষাকৃত গ্রামাঞ্চলের মানুষ। কিন্তু এরা দক্ষিণপন্থী এই অর্থে যে, এদের প্রধান রাগ হচ্ছে, বড়–বড় শহরের ফিনান্সিয়াল হাউজ, বড়–বড় শহরের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা, বৈভব এবং বিদেশিদের আনাগোনার বিরুদ্ধে। বিদেশি বলতে সেখানে ধনী বিদেশিও প্রচুর, আবার সাধারণ যারা কাজ করে কিন্তু বিদেশি, বিদেশ থেকে আসা মানুষ তারা। টি পার্টির বক্তব্য ছিলো, বিদেশ থেকে আসা লোকেরা আমাদের কাজকর্মগুলো দখল করে নিচ্ছে। এই ইমিগ্র্যান্ট বিরোধী মনোভাব, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেষ অব্দি ট্রাম্পের মতো একজন জনবাদী বা পপুলিস্ট নেতার পুরো রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম। পশ্চিম ইউরোপে এরকম একাধিক দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী— দু’রকম পপুলিস্ট আন্দোলন আমরা দেখতে পাই। দক্ষিণপন্থী বলতে প্রধানত ইমিগ্র্যান্ট বিরোধী মত, ইসলাম বিরোধী মত— এটাই প্রধানভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তাদেরকেই তারা প্রথম শত্রু বলে চিহ্নিত করে। আবার বামপন্থীও আছে, বামপন্থী পপুলিস্ট। তারা পপুলিস্ট এই অর্থে যে, পুরোনো যে সমাজবাদী দলগুলো, কমিউনিস্ট দলের যেরকম সংগঠন, সেরকম সংগঠন তাদের থাকে না। কিন্তু তারা সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষ, অপেক্ষাকৃত সাধারণ মধ্যবিত্ত, তাদের জন্য সরকার আরও কিছু কল্যাণমূলক কাজ করুক— এই দিকে তাদের ঝোঁক বেশি। এটা হচ্ছে পাশ্চাত্যে যে পপুলিজম, তার ছক।

এইখানে আমি ছোট করে একটা তত্ত্বের কথাই বলি। পপুলিজম বিশ্লেষণ করতে গেলে, জনবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কোথায়, এখানে একজন বিশেষ তাত্ত্বিকের কথা আমি বলবো। আর্নেস্তো লাকলাউ। ইনি ছিলেন আর্জেন্টিনার মানুষ, কিন্তু আর্জেন্টিনা থেকে বিতাড়িত। ইংল্যান্ডে অধ্যাপনা করতেন। উনি On Populist Reason বলে একটি বই লিখেছিলেন ২০০৫ সালে। তাতে তিনি পপুলিজমের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক— তার একটা বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণটা মূলত এইরকম। উনি বলছেন যে, দু’ধরনের রাজনৈতিক পন্থা হতে পারে। একটিকে উনি বলছেন ডেমোক্র্যাটিক অর্থাৎ যেটা একটা ডিফারেন্সিয়াল লজিকে চলে। ডিফারেন্সিয়াল লজিক বলতে ঠিক আগে আমি যেটা বলছিলাম, অর্থাৎ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের দাবি থাকতে পারে। সমস্ত দাবি সরকারের পক্ষে মেটানো সম্ভব হয় না। সুতরাং যেই যেই দাবিগুলো রাজনৈতিকভাবে মেটানো সম্ভব ও মেটানো প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে, তার একটা কস্ট–বেনিফিট হিসেব থাকে। এই দাবিটা মেটাতে কত খরচ পড়বে, এবং তা থেকে আমাদের রাজনৈতিকভাবে কতটা সুবিধা হবে, এইরকম একটা হিসেব থাকে। তার ভিত্তিতে কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর দাবি মেটানো হয়, সকলের দাবি মেটানো যায় না। এইটা হলো লজিক অফ ডিফারেন্স বা ডিফারেন্সিয়াল লজিক অর্থাৎ পৃথকীকরণের নীতি। কিন্তু এর ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকবে, যাদের দাবি মেটানো হলো না। এই যে মেটানো হলো না, তার ফলে কিন্তু তাদের মধ্যে এইরকম একটা ধারণার জন্ম হতে পারে যে, যদিও আমাদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর দাবি স্বতন্ত্র, কিন্তু আমরা সকলেই একই অবস্থায় আছি, তার কারণ আমাদের একজন শত্রু আছে যে আমাদের দাবি অস্বীকার করছে। অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী বা এলিট। আমরা সকলেই সমানভাবে সেই শাসক এলিটদের দ্বারা অত্যাচারিত। এই যে এক ধরনের সমীকরণের নীতি, এটাকে লাকলাউ বলছেন, লজিক অফ ইকুইভ্যালেন্স। এই সমীকরণের নীতি থেকে পপুলিজমের জন্ম হয়। অর্থাৎ জন্মলগ্নে কিন্তু পপুলিজম একটা বিরোধী রাজনীতি থেকে আসে। একটা কোনো প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠী আছে আর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে যারা নানা রকম দাবি করছে। যাদের দাবিগুলো মিটলো না, সেইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি এই ধারণা সৃষ্টি করা যায় যে তারা সকলেই আসলে এক অবস্থায় কারণ তারা সকলেই একই শত্রু দ্বারা অত্যাচারিত, তাহলেই জনবাদী রাজনীতির জন্ম হয়। এইটা হলো লাকলাউ–এর বিশ্লেষণ। এর পরে উনি বিশ্লেষণ করে বলছেন যে, ধারণাটা সৃষ্টি করা যায় কী করে। সব সময় সব ক্ষেত্রে চেষ্টা করলেও এই ধারণা তৈরি করা যায় না। ধারণাটা সৃষ্টি হয় রেটরিকের মাধ্যমে। অর্থাৎ একটা বয়ানের মধ্যে, এক ধরনের অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্যে, কিছু কল্পকাহিনীর সৃষ্টি করার মধ্যে, কিছু পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নাটক সৃষ্টি করতে হয়। এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের ভাবাবেগকে স্পর্শ করতে হয়। তাহলেই এই জনবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ জনবাদী রাজনীতির মধ্যে কিন্তু উনি বারে বারে যদিও রিজন কথাটা বলছেন, কিন্তু এর যে ইমোশনের দিকটা, সেটা কিন্তু প্রধান। কারণ শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অ্যাকশন যখন হবে, বিশেষ করে যদি আমরা একটা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কথা বলি, তাহলে সেখানে এই যে ইমোশনের দিকটা, এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বারেবারে তিনি এই দিকটাতে, এই রেটরিকাল তথা আলঙ্কারিক দিকটাতে জোর দিয়ে বলছেন যে, জনবাদী রাজনীতির আসল চরিত্র এখানেই লুকিয়ে আছে।
এইবারে আমি প্রাচ্যের তথা এশিয়া–আফ্রিকার পপুলিজম প্রসঙ্গে আসি। বিভিন্ন দেশে এই পপুলিস্ট রাজনীতি, পপুলিস্ট নেতা, পপুলিস্ট দল আমরা দেখেছি। এখানে কতগুলো সাধারণ কথা আমি বলি। ভারতবর্ষের অনেক উদাহরণ আমি দিতে পারি। কিন্তু তার মধ্যে আমি এক্ষুণি যাচ্ছি না। আমি সাধারণভাবে এই জনবাদী রাজনীতির কতগুলো চরিত্র এবং বিশেষ করে জনবাদী নেতার ভূমিকা নিয়ে বলব। জনগণ একদিকে এবং কোনো এক শোষক গোষ্ঠী যারা জনগণের শত্রু অন্যদিকে— এই ধারণাটা সৃষ্টি করার মধ্যে একজন নেতার ভূমিকা অনেকক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। জনগণের যে তথাকথিত ঐক্য, এই ঐক্যটা প্রতিষ্ঠিত হয় একজন নেতার ব্যক্তির মধ্যে। তার ব্যক্তির মধ্যে জনগণের ঐক্য প্রতিফলিত হয়। আবার বলছি, যে কেউ জনবাদী নেতা হওয়ার চেষ্টা করলেই যে তিনি তা হতে পারবেন, তা নয়। কোন অবস্থায় কী কারণে তা সম্ভব হয়, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। দু’নম্বর যেটা বড় কথা, যা প্রাচ্যে বহু জায়গায় দেখা গেছে যে, একটা বিরোধী জায়গা থেকে এই জনবাদী নেতা বা দল, তারা শাসকদল হয়ে গেল। তারা নির্বাচনে জিতে সরকার প্রতিষ্ঠা করল। লাকলাউ–এর আলোচনাতে কিন্তু এই দিকটাতে উনি খুব জোর দেননি। তার কারণ, ওনার মত ছিলো যে, সরকারে আসার পরে জনবাদী রাজনীতি বেশিদিন টিকতে পারে না। কেননা জনবাদী রাজনীতির ভিত্তিটা একমাত্র বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেতে পারে। একবার সরকারে চলে এলে অবধারিতভাবে সেই ডিফারেন্স বা পৃথকীকরণের নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কিছু কিছু গোষ্ঠীকে সুযোগ–সুবিধা দেওয়া যাবে, বাকিদের দেওয়া যাবে না। তাতে আবার একটা নতুন বিরোধিতা তৈরি হয়ে যাবে। একটা পপুলিস্ট দল, সে যদি বেশি দিন ক্ষমতায় থাকে, সে আর পপুলিস্ট থাকতে পারবে না বরঞ্চ তার বিরুদ্ধে একটা অন্য কোনো পপুলিস্ট রাজনীতি, বিরোধী রাজনীতি তৈরি হয়ে যাবে। সুতরাং লাকলাউ–এর ধারণায়, পপুলিস্ট রাজনীতি শাসন ক্ষমতায় এসে বেশিদিন টিকতে পারে না।
কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে, আফ্রিকা–এশিয়ার অন্য দেশ থেকেও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে যে, এই জনবাদী রাজনীতি শুধু যে একজন নেতার নেতৃত্বেই দীর্ঘ দিন শাসন করেছে শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এক নেতা চলে গিয়েছেন কিন্তু দল সেই নেতার বদলে আরেকজন নেতা নির্বাচন করেছে। অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে কিন্তু ওই জনবাদী দল তার জনবাদী চরিত্র বজায় রেখেছে, এরকম উদাহরণ অনেক জায়গায় পাওয়া যাবে। এখানে সবচেয়ে যেটা ভেবে দেখার এবং অনেকে বলবেন দুশ্চিন্তার জায়গা, সেটা হলো একদিকে যেরকম এই জনবাদী রাজনীতির ফলে খানিকটা জনকল্যাণমূলক কাজের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে নানা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে জনবাদী নেতৃত্বের মধ্যে স্বেচ্ছাচার আর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সম্ভাবনাও প্রবল। একটা জিনিস যেরকম আমি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বলতে পারি। এই জনবাদী রাজনীতির সম্পূর্ণ প্রশাসনিক একটা দিক আছে, অর্থাৎ সরকার খরচ করবে, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য নানা প্রকল্পের মাধ্যমে খরচ করা হবে। এটা কিন্তু কখনোই ইউরোপের ওয়েলফেয়ার স্টেটের মতো ব্যবস্থা নয়। কারণ ওয়েলফেয়ার স্টেটের মতো সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, সকলের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, আমাদের দেশে কোনো সরকারের সেরকম রাজস্ব নেই যে তারা সেটা করতে পারে। সুতরাং কিছু লোককে দেওয়া হবে, কিছু লোককে দেওয়া হবে না। এইখানে যাদের প্রয়োজন বেশি, তাদের জন্য যাতে দেওয়া হয়, এই ধারণাটা কিন্তু এখন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে। সবরকম দল, তাদের অন্যান্য রাজনৈতিক মত যাই থাকুক না কেন, সকলেই এখন মোটামুটিভাবে প্রশাসনিক পপুলিজম, অর্থাৎ সরকারি খরচের দিক থেকে এই ধরনের এক্সপেন্ডিচার, মেনে নিয়েছে। নানা রকম প্রকল্প, সেটা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যেই হোক, মহিলাদের জন্যেই হোক, শিশুদের জন্যেই হোক, বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য প্রকল্প, বিভিন্ন ধরনের স্কুল শিক্ষা প্রকল্প, খাদ্য বা বাসস্থান ইত্যাদির জন্য নানারকম সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা, এগুলো এখন ব্যাপকভাবে সব দলের সরকার করে থাকে।

অর্থাৎ, জনবাদের এই দিকটা এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত হয়ে গেছে। অন্তত পৃথিবীর এই অংশটাতে যেখানে আমরা বাস করি। কিন্তু এর অন্য যে রাজনৈতিক মতবাদের দিক, অর্থাৎ নেতার অবস্থান, নেতার সঙ্গে তার সমর্থকদের সম্পর্ক, এই দিকটার কিন্তু একটা অত্যন্ত বিশিষ্ট চরিত্র আছে জনবাদী রাজনীতিতে। এই নেতা কিন্তু এক অর্থে সার্বভৌম নেতা। অর্থাৎ জনগণের সার্বভৌমত্ব যেন তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, এইরকম একটা ধারণা। তিনি সার্বভৌম নেতা, জনগণের কল্যাণের জন্য বা জনগণের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য তিনি জনগণের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। নানারকম আইনকানুনের বেড়াজাল, যার মাধ্যমে এতদিন অব্দি এলিট শাসকশ্রেণি তারা সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে, সেই আইনকানুনের পাশ কাটিয়ে, সেই বেড়াজাল ভেঙে, দরকার হলে আইন ভেঙে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করে দেবেন। এই ধারণাটা কিন্তু জনবাদী রাজনীতির মূলে রয়েছে। উদারনৈতিক রাজনীতি বা সাংবিধানিক রাজনীতির যেটা মূল কথা, যে শেষ অব্দি আউটকাম বা ফলটা ভালো হলো কি হলো না সেটা অত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু আইনের যে প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াটা বজায় রাখতে হবে। তার কারণ তুমি প্রক্রিয়া ভেঙে যদি শেষ অব্দি একটা ভালো ফলও পাও, ভবিষ্যতে কিন্তু তোমাকে তার জন্য খেসারত দিতে হবে। কারণ আইনের নিরপেক্ষ প্রক্রিয়াটা তুমি নষ্ট করে ফেললে। এর পরে তুমি চাইলেও বিচার পাবে না। এই যে সাংবিধানিক ধারণাটা, জনবাদের রাজনীতি কিন্তু এটা স্বীকার করে না। স্বীকার না করার একটা বড় কারণ এই যে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাই হচ্ছে যে ওসব আইন–কানুন আসলে বড়লোকদের ব্যাপার। ওটা তাদের সুবিধার জন্য তৈরি করা, ওখানে আমরা সাধারণ মানুষ গিয়ে তো কিছুই করতে পারবো না। যদি কোনো কারণে আমরা আইন–কানুন করতে যাই, থানা–পুলিশ করতে যাই, কোর্ট–কাচারি করতে যাই, শেষ অব্দি দেখা যাবে যে বড়লোকেরা বড় বড় উকিল নিয়ে আসবে, তারাই জানে কী করে কী করতে হয়, আমরা তো জানি না, শেষ অব্দি আমরাই ভুগি, আমাদের ভাগ্যে কিছু জোটে না। তার বদলে আমরা এমন একজন নেতা যদি বাছতে পারি এবং তাকে যদি শাসন ক্ষমতায় বসাতে পারি, যিনি প্রয়োজন হলে সমস্ত আইন–কানুন ভেঙেও আমাদের জন্য কিছু করে দেবেন, একমাত্র তাহলেই আমরা কিছু পাবো।
এই ধারণাটা জনবাদী রাজনীতির মধ্যে একটা বিপজ্জনক সম্ভাবনা। এই বিপদটার জন্য জনবাদী রাজনীতির সমালোচনা করা হয়। তাতে দুটো সমালোচনা বড়। একটা হচ্ছে, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং ক্ষমতার আরবিট্রারি অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ, অর্থাৎ আইন–কানুনের তোয়াক্কা না করে, নিজের পছন্দ মতো কোনো কাজ করতে পারা। এই ক্ষমতাটা সংবিধান কখনো কোনো শাসককে দেয় না। সংবিধান সবসময় বলবে যে শাসক, তিনি যতই মানুষের ভালো করতে চান, সেটা আইন মেনে করতে হবে। কিন্তু জনবাদী নেতারা মনে করেন, আমার আইন মানার দরকার নেই, কারণ আমি যেটা করতে চাইছি, সেটা মানুষের ভালো করার জন্য। এই ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সাংবিধানিক ব্যবস্থাটা কিন্তু ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা হয়।
জনবাদী নেতৃত্বের আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। এই জনবাদী নেতা কিন্তু শেষ অব্দি ডিক্টেটর হন না কখনো। এটা একটা লক্ষ্য করার মতো বিষয়। সম্প্রতিকালে নানা দেশে অনেক অথরিটেরিয়ান একনায়কও দেখা গেছে। কিন্তু তারা সকলেই কিছু দিন পরপর একটা করে নির্বাচন করান। এবং নির্বাচনে বিরোধীও থাকতে হয়। এবং সেই বিরোধীদের উনি পরাস্ত করে জনগণের সমর্থন নিয়ে যে আবার ক্ষমতায় এলেন, এটা একজন জনবাদী নেতাকে বারেবারে প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ তিনি দেখাতে চান যে তার ক্ষমতার উৎস হলো যে তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপে বহু জায়গায় এমন ঘটনা হয়েছে, এমনকি উনিশশত পঞ্চাশ–ষাটের দশকেও লাতিন আমেরিকার বহু জায়গায় হয়েছে, আফ্রিকার বহু জায়গায় হয়েছে যে একজন নেতা ক্ষমতায় এলেন, তারপর নির্বাচন–টির্বাচন সব তুলে দিলেন। দরকার নেই। তিনি যেন চিরস্থায়ী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। এমন ঘটনা কিন্তু সাম্প্রতিককালে বেশি দেখা যাবে না। দেখা যাবে না, তার কারণ এই পপুলিজমের ছকটা, যেখানে বারেবারেই তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমার ক্ষমতার নৈতিক ভিত্তি হচ্ছে জনগণের সমর্থন। সেই সমর্থনটা তাকে প্রদর্শন করতে হবে কিছুদিন পরপর। এখানেই জনবাদী রাজনীতির দ্বিতীয় সমালোচনা চলে আসে। সেটা হলো যে, এই জনবাদের কোনো বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের প্রকল্প থাকে না। এর সবটাই হচ্ছে পরবর্তী নির্বাচন জেতার জন্য কোন কোন গোষ্ঠীকে কোন কোন সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন, সেই প্রশ্ন। সেটা সবসময়ই যে সাধারণ জনস্বার্থের বিরোধী হবে, এমন হয়তো নয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে একটা সমাজ পরিবর্তনের কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প জনবাদী রাজনীতির থাকে না। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই জনবাদী রাজনীতি দক্ষিণপন্থী না বামপন্থী, এটা অনেকক্ষেত্রেই বোঝা মুশকিল হয়ে যায়, কারণ তাদের মতবাদের দিক থেকে অনেক জনবাদী দল বা নেতাকে মনে হবে খুব দক্ষিণপন্থী কিন্তু তারাই হয়তো অনেক রকম নীতি গ্রহণ করবে যেগুলো আসলে বামপন্থীদের নীতি। কিন্তু সেইসব নীতি তাদের নিতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তারা ওইভাবে কোনো একটা দীর্ঘস্থায়ী সমাজ পরিবর্তনের প্রকল্পের দিক থেকে এটা ভেবে দেখছে না। তাদের কাছে হিসেবটা হচ্ছে, এর থেকে নির্বাচন বা জনসমর্থনের দিক থেকে কতটুকু সুবিধা। এই হিসেব করে জনবাদের রাজনীতি চলে।এতগুলো কথা আমি মোটামুটি বললাম। প্রথম কথা, জনবাদী রাজনীতির সূত্র হচ্ছে একটা নির্বাচনী গণতন্ত্র। সেই নির্বাচনী গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে একটা বিশেষ ধরনের জনবাদী রাজনীতির কী করে উদ্ভব হয়, সেটা আমি বললাম। আমি আরও বেশি করে বলছি যে, এই জনবাদী রাজনীতির যে বিভিন্ন রকমের প্রকাশ, এটা কিন্তু পাশ্চাত্যের তুলনায় এশিয়া–আফ্রিকার দেশগুলোতে অনেক বেশি দেখা গেছে। অনেক সময় আমার মনে হয় যে, এই ট্রাম্পের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনবাদী রাজনীতির যে প্রকাশ, পশ্চিম ইউরোপের অনেক জায়গায় যা এখন দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশে এই অভিজ্ঞতাটা আমরা অনেকদিন ধরে ভালোভাবে সঞ্চয় করেছি। সুতরাং এই ঘটনাগুলো পাশ্চাত্যের কাছে যতটা অত্যাশ্চর্য মনে হয়, আমাদের কাছে মোটেই অত আশ্চর্যের লাগে না। এরকম তো আমরা কত দেখেছি। কিন্তু কেন গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে এই ধরনের জনবাদী রাজনীতির উদ্ভব হতে পারে সেটাই আমি খানিকটা বলার চেষ্টা করলাম। এবারে আপনারা যদি প্রশ্ন করেন আমি অতি অবশ্যই উত্তর দেবো।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
প্রশ্ন ১: সান্তাল মউফ, আর্নেস্তো লাকলাউ, আকিল বিলগ্রামী প্রমুখ চিন্তকরা পপুলিজমকে এক্সক্লুসিভলি নেগেটিভ কনোটেশন হিসেবে মানতে চান না। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন হাজির হয়, গণমুখী রাজনীতির জন্য পপুলিজম কি আবশ্যিকভাবে খারাপ? নাকি পপুলিজম গণমুখী ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতিরও কৌশল হতে পারে?
পার্থ চট্টোপাধ্যায়: আমি তো বললাম যে কৌশল হতে পারে। পপুলিজম গণমুখী রাজনীতির কৌশল হতে পারে এবং বহু জায়গাতেই তা হয়েছে। বিশেষ করে যে কথাটা আমি আরও বেশি করে বললাম, জনবাদী রাজনীতির মধ্যে থেকে যেসব ধারণার জন্ম হয়েছিলো, অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের জন্য বিশেষ প্রকল্প, বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকির ব্যবস্থা, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য প্রকল্প, শিশুদের জন্য প্রকল্প, তাদের স্বাস্থ্যের জন্য প্রকল্প— এই ধরনের প্রকল্পগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু জনবাদী রাজনীতির চাপে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি সম্পূর্ণ প্রশাসনিক পরিকল্পনার কথাই শুধু বলছি না। রাজনীতির মাধ্যমে যখন এগুলোকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হয়েছে, বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাবে কোনো জনবাদী দল বা জনবাদী নেতা বা কোনো জনবাদী সরকারের চাপে এই জিনিসগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। এবং বহু জায়গায় এগুলো এখন সাধারণভাবেই গৃহীত। সুতরাং জনবাদ নিশ্চয়ই গণমুখী রাজনীতির কৌশল হতে পারে। কিন্তু আবার বলছি এটা কৌশল। আমার মতে জনবাদী রাজনীতির পরিসরের মধ্যে থেকে কোনো ব্যাপক দীর্ঘস্থায়ী সমাজ পরিবর্তনের প্রকল্প হতে পারে না। তাহলে জনবাদী রাজনীতির বাইরে যেতে হবে। সেই প্রকল্প প্রগতিশীল হোক বা অন্যরকম কিছু হোক, ব্যাপক সমাজ পরিবর্তনের প্রকল্প যদি হয় তাহলে কিন্তু জনবাদী রাজনীতির থেকে আরও বেশি কিছু করতে হবে। সেই রাজনীতি শুধুমাত্র পরবর্তী নির্বাচনে জিতবো, এই হিসেবের মধ্যে, এই কৌশলের মধ্যে থাকলে হবে না।
প্রশ্ন ২: বর্তমান দুনিয়ায় আমরা দেখতে পাচ্ছি; যে রাষ্ট্রকাঠামোগুলা ‘লিবারেল ডেমোক্রেটিক স্টেট’ হিশেবে পরিচিত ছিলো, সেই সবগুলো রাষ্ট্রেই ‘পপুলিস্ট সুপার লিডার’ খ্যাত স্বৈরাচারী শাসকদের উত্থান দেখা যাচ্ছে। এখন আমার প্রশ্নটা হলো, প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমকে ব্যবহার করে এত সহজে কী করে ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী রাজনীতি নিজের পরিসর তৈরি করতে পারছে?
পার্থ চট্টোপাধ্যায়: পাশ্চাত্যের কথা যখন বলছি, একটা নিওলিবারেল প্রশাসনের সময় গিয়েছিলো, বিশেষ করে ১৯৮০–৯০, ২০০০–এর সময় – এই বছর তিরিশের মতো। সেই সময়টাতে আমরা দেখেছি যে সাধারণভাবে এই দেশগুলোতে একটা ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সময়। পুরোনো শিল্প, যন্ত্র শিল্প, ম্যানুফ্যাকচারিং – সেইগুলো সমস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ব্রিটেন থেকে সরে গেল। বড় বড় পুরোনো ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেল। এইসব শিল্পোৎপাদন অন্য দেশে চলে গেল। মানে আমেরিকান কোম্পানি, কিন্তু তারা আর আমেরিকাতে মোটর তৈরি করে না। তারা কেউ মেক্সিকোতে গিয়ে করে, কেউ অন্য কোনো দেশে গিয়ে করে, বিদেশী কোম্পানির উৎপাদনের একটা বড় জায়গা হয়ে গেল চীন। বহুজাতিক কোম্পানিরা, তারা চীনে তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে চলে গেল। অন্যান্য বহু দেশে এই ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ পুরোনো যে শিল্প–শ্রমিক ভিত্তিক অর্থনীতি ছিলো, সেগুলো আস্তে–আস্তে ওই দেশ থেকে চলে গেল। তার ফলে একটা বড় অসাম্য তৈরি হলো। এই অসাম্য মেটানোর একমাত্র উপায় ছিলো, ফিনান্সিয়াল দিক থেকে, অর্থাৎ ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স, স্টক মার্কেট, আন্তর্জাতিক লেনদেন – এইখান থেকে ফিনান্সিয়াল যে মুনাফা, তার খানিকটা অংশ, তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করল। বিশেষ করে, সস্তায় চীন থেকে বা ভিয়েতনাম থেকে, বাংলাদেশ থেকে জিনিস তৈরি করে আমেরিকান কোম্পানিরা আমেরিকার সাধারণ মানুষদের সস্তায় বিক্রি করতে লাগলো। ধরুন বাংলাদেশে বিখ্যাত ব্র্যান্ডের জামাকাপড় তৈরি হচ্ছে। আমি কিছু দিন আগে একটা টেলিভিশন প্রোগ্রামে দেখছিলাম, যে আমেরিকায় যেখানে লিভাইস জিন্স তৈরি হতো, সেই শহরের লোকেদের জিজ্ঞেস করছে যে এখানে যদি তৈরি হয়, একটা জিন্সের কত দাম হবে? আর এখন তোমরা ওয়ালমার্টে জিন্স কততে পাও? সবাই বললো, হ্যাঁ, এখন অনেক তফাৎ হয়ে গেছে, কারণ বিদেশ থেকে তৈরি করা লিভাইস ব্র্যান্ডের জিন্স এখন অনেক সস্তায় পাওয়া যায়। তার ফলে একজন সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের স্তর, শিল্পোৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেটা ধরে রাখতে পারা গিয়েছিলো, যদিও আগেকার যুগে তার চাকরির যে রোজগার ছিলো, সেই রোজগার তার নেই। এই অসাম্যটা হঠাৎ ভীষণভাবে প্রকট হয়ে গেল, ওই ফিনান্সিয়াল জগতটা যখন ক্র্যাশ করল। ওই ক্র্যাশের পরে, ২০০৯–১০ সাল থেকে এই যে ধারণাটা ছড়িয়ে পরল যে, একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, তারা সমস্ত মুনাফা খেয়ে ফেলছে আর আমাদের ভাগে কিছু থাকছে না। আমরা আমেরিকাতে দেখেছি, দক্ষিণপন্থী ট্রাম্প এই ধারণাটার সুযোগ নিয়ে একটা দক্ষিণপন্থী জনবাদী রাজনীতি তৈরি করতে পারলো। ইউরোপের অনেক দেশে কিন্তু এই অসাম্যের প্রতিবাদে বামপন্থী রাজনীতিও হয়েছে। গ্রিসে যেরকম সিরিৎসা বলে একটা দল আছে, স্পেইনে পডেমস বলে একটা দল আছে – তারা এখন ক্ষমতায় এসেছে। ইতালিতে ফাইভস্টার বলে একটা দল আছে, তারাও এখন সরকারে এসেছে। এরা জনবাদী কিন্তু ওই অর্থে দক্ষিণপন্থী নয়। এরা ওরকম বিদেশি বিরোধী, সমস্ত ইমিগ্র্যান্ট চলে যাও – এইসব কথা বলে না। সুতরাং বামপন্থী পপুলিজমও আছে অনেক দেশে। আবার দক্ষিণপন্থীও আছে। দু’রকমই থাকতে পারে। কিন্তু এর ভিত্তিটা হচ্ছে, যে ধরনের স্থিতাবস্থার মধ্য দিয়ে নিওলিবারেল রাজনীতি চলছিলো, সেই স্থিতাবস্থাটা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। এবং তার একটা বড় বহিঃপ্রকাশ, যেটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাবেন, যে পুরোনো যে রাজনৈতিক দলগুলো ছিলো, সেগুলোর ভেতর প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রায় ভেঙে দু–তিন টুকরো হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। সেটা আপনি আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে দেখবেন, ইংল্যান্ডের কনজারভেটিভ বা লেবার পার্টির মধ্যেও দেখবেন, ফ্রান্সে যে সোশ্যালিস্ট দল, সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। এই যে পুরোনো বড় বড় দলগুলো যারা এতদিন ধরে ক্ষমতা ধরে রেখেছিলো, রেপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্টের কাজ করছিলো, সেই সংগঠনগুলো সমস্ত ভেঙে গেছে। এইখানেই হয় দক্ষিণপন্থী না হয় বামপন্থী জনবাদ, জনবাদী রাজনীতির জায়গা তৈরি হয়েছে।

প্রশ্ন ৩: উন্নয়ন প্রপঞ্চের নিরিখে পশ্চিমকে এতকাল অন্যসব দেশগুলো মডেল মেনে এসেছে, পশ্চিম হতে চেয়েছে। এরপর সেই পশ্চিমা দেশগুলোতে পপুলিজমের বিস্তারণে ট্রাম্প ও জনসনের মতো মানুষেরা ক্ষমতায় আসছে। প্রতিফলে গনতান্ত্রিকভাবে দুর্বল দেশগুলোতে পপুলিজম ও স্বৈরতান্ত্রিকতার মিশেলে নতুন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। পপুলিজমের বৈশিষ্ট্য মেনে একদিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানাদির ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে ব্যক্তিবিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, রাজনৈতিক বহুত্ববাদ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, পপুলিজমের আরেকটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে জনগণের ইচ্ছের গুরুত্ব থাকার যে শর্ত আছে– সেটাকে বেমালুম অস্বীকার করা হচ্ছে– বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে। এতে করে গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারের নানান প্রশ্নে উন্নত সব দেশ ও তাঁদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যারা আগে এ ধরনের বাস্তবতায় আপাত দৃষ্টিতে জনগণের স্বার্থে নানাবিধ প্রয়াস পেত– সেগুলোর কার্যকারিতা ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে। তো, এমত বাস্তবতায় সম্মিলিত মানুষের অগ্রগতির প্রশ্নে অর্থাৎ আরাধ্য মুক্তির প্রশ্নে কোন ধরনের পথ পাথেয় বিবেচিত হতে পারে?
পার্থ চট্টোপাধ্যায়: এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করলেন। এখানেই আমার ওই প্রশ্নটা উঠছে যে, যেহেতু জনবাদী রাজনীতির কোন বৃহত্তর সমাজ পরিবর্তনের দায় নেই, সেই জন্যে বহু ক্ষেত্রেই মানবাধিকার বা নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা, সমস্তটাই সুবিধাবাদের ওপর চলে। অর্থাৎ আমি সাংঘাতিক রকমের অপকর্ম করতে রাজি আছি যদি শেষ অব্দি কোথাও আমার একটা রাজনৈতিক সুবিধা হয়। আমি সেক্ষেত্রে মানবাধিকারের কোন তোয়াক্কাই করব না যদি নির্বাচনের দিক থেকে আমার সুবিধা হয়। আপনি একটা জিনিস বহু জায়গায় লক্ষ্য করবেন, আমি ভারতবর্ষের কথাই বলি। যেমন, আমি একটা ধর্মীয় গোষ্ঠী, যারা সংখ্যালঘু, তাদের আমি চিহ্নিত করলাম যে, এদের জন্যই আমাদের সমস্ত অসুবিধা, সুতরাং এদের খানিকটা শায়েস্তা করো। এটাতে নির্বাচনী রাজনীতিতে যদি আমার সুবিধা হয়, অর্থাৎ আমি একটা মেজরিটি মতকে সংগঠিত করতে পারি, আমার তাতে সুবিধা। সুতরাং এই বিভাজনের রাজনীতি সে করবে। তার জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলো কি হলো না, সেটা সে খুব একটা তোয়াক্কা করবে না। এইবারে অসুবিধাটার কথাটা আপনি যেটা বললেন, এটা খুবই ঠিক কথা। যে ধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক মত, যেটা কোন এক সময় হয়তো অনেকটা প্রভাবশালী ছিলো, এই প্রভাব অনেক কমে এসেছে। দু’দিক থেকে কমে এসেছে। প্রথম কথা, আপনি এই ট্রাম্পের যুগে তো দেখতেই পেলেন যে, একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা যে সরকারী ক্ষমতার শীর্ষে – সে নিজেই এই ধরনের মানবাধিকার ইত্যাদির কোনো গুরুত্ব দেয় না। সুতরাং তার নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মানবাধিকার রক্ষা করো, এই কথা বলা সম্ভবই ছিলো না, সে চাইতোও না করতে। আর একবার যখন ঘটনাটা ঘটে যায়, তারপরে কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর পেছনে যে রাজনৈতিক শক্তি থাকে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধেও একটা বড় রকমের প্রশ্নচিহ্ন দাঁড়িয়ে যায়। আর যারা এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে, সেই শাসকেরা তখন সেই সুযোগটা নিয়ে বলবে ওই আন্তর্জাতিক মতের বিশ্বাসযোগ্যতা কী? ওদের কথা আমাদের শুনতে হবে কেন? না শুনলে তাদের যে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, তাও হয়তো নেই। এখানে আবার মায়ানমার বা বার্মার প্রসঙ্গটায় আসে। সেখানকার ঘটনা তো এখন রোজই আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, সারা পৃথিবী চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে এরকম একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, অথচ কিছু করার উপায় নেই। কেউ কিছু করতে চাইছে না। সুতরাং, এই অসুবিধাটা তো আছেই। তবে এটা যে শুধুমাত্র জনবাদী রাজনীতির সমস্যা, এটা আমি বলবো না। কথাটা একটু অন্যভাবে বলি। জনবাদী রাজনীতির মধ্যে এই যে স্বল্পমেয়াদী ভাবনা, এটা সম্পূর্ণ কৌশলগত ভাবনা। নীতিগত ভাবনা এই ধরনের রাজনীতিতে খুব কম। সেখানে কৌশলগত ভাবনাই অনেক বেশি প্রবল। সেই কৌশলগত চিন্তা এখন পশ্চিমের সরকারগুলোর মধ্যেও ঢুকে গেছে। সুতরাং আপনি যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলছেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যাওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়। নীতিগত দিক দিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, সেটা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, এরকম একটা অবস্থায় আমরা পৌঁছে গেছি। এতদিনে যা হয়েছিলো, তার থেকে অনেকটাই হয়তো আমরা পিছিয়ে গেলাম। নতুন করে ফের শুরু করার জায়গায় চলে এসেছি।
প্রশ্ন ৪: প্রচলিত গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রাবল্য ঘটে, তা নিরসনে কি কি প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ দেখছেন? ক্রমাগতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক (সমগ্র জনগোষ্ঠীর) প্রতিনিধিত্বের জনসাধারণের জন্য সেবা কাঠামো (বিচার বিভাগসহ সরকার ও প্রশাসনের) কীভাবে গড়ে উঠতে পারে বলে আপনার ধারণা? এটা কি আদৌ প্রচলিত গণতন্ত্রে করা সম্ভব হচ্ছে, আপনার মত কী?
পার্থ চট্টোপাধ্যায়: এটা তো খুব বড় প্রশ্ন করলেন। এতটা বড় প্রশ্নের উত্তর যে আমি চট করে বলে দিতে পারবো, মোটেই আমি সেই দাবি করবো না। আমি যেটা বারেবারে বলার চেষ্টা করছি যে, প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের বাইরে অন্য কোনো জায়গায় তো বললেই রাতারাতি চলে যেতে পারি না। সুতরাং এখন যেটুকু গণতন্ত্র আছে তার মধ্যে থেকেই একটা কোন নতুন দিকে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে বার করতে এবং সেইদিকে যাবার চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টাটা কোন কোন দিকে জোর দিলে আরও সহজে পাওয়া যাবে, এটাই আসলে ভেবে দেখা এবং খানিকটা কাজ করে দেখার ব্যাপার আছে। সুতরাং আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি যে, রাজনীতিকে শুধুমাত্র কৌশলগত দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, এর মধ্যে যে নীতিগত দিক আছে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে আর কাজ করতে হবে। তাতে কিন্তু আজ করলাম, কালকেই তার ফল পেয়ে যাবো, এই ঘটনাটা ঘটবে না। এখানে এমন প্রচেষ্টার প্রয়োজন, যেটা হয়তো শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, যেটা আরও ব্যাপকভাবে সামাজিক বিষয়। সেটা সাংস্কৃতিক উৎসব হতে পারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠনের মধ্যে হতে পারে। অর্থাৎ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে সমবেত একটা জনগোষ্ঠীর ধারণা, সমবেতভাবে কাজ করার ধারণা, এবং সমবেতভাবে সহাবস্থানের ধারণা— এই ধারণাগুলো আরও গভীরভাবে কী করে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন, কর্মী এবং কাজকর্মের কী ধারণা হতে পারে, এগুলো অনেক বেশি করে ভাবার প্রয়োজন। সরাসরিভাবে রাজনৈতিক দিকটার যে অসুবিধা, যেটা আপনি প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রসঙ্গে বলছেন, সেটা হলো যে তাতে নির্বাচনে কী হবে, এই প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দিতে বাধ্য। আমার কাজটা হচ্ছে কি হচ্ছে না, সফল হলাম কি হলাম না, প্রচলিত গণতন্ত্রে তার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে আমি নির্বাচনে কি ফল পাবো। তাই এর বাইরে যেটা সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজ নয়, কিন্তু রাজনীতি বা রাজনৈতিক মানুষের চেতনার দিক, তার চিন্তাভাবনার দিক এবং তার কাজ করার প্রক্রিয়ার দিক— এই ভিত্তিগুলো যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে, যেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেই ভিতগুলো তৈরি হচ্ছে, সেইখানে গিয়ে কাজ করার কথাটাতে আমি আরও বেশি করে জোর দিতে চাই। সেইখানে না গেলে কিন্তু এই নীতিগত প্রশ্নগুলোকে সামনে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না।
প্রশ্ন ৫: স্বৈরাচারী বা কর্তৃত্ববাদী শাসক মাত্রই কি বর্তমান বিবেচনায় পপুলিস্ট হিশেবে গণ্য হবে? এই প্রশ্ন উঠছে কারণ বাংলাদেশসহ এমন বেশ কয়েকটি গণতান্ত্রিক রীতি–নীতি, প্রতিষ্ঠান সম্বলিত রাষ্ট্রে এক নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যেখানে নির্বাচন হয়ে উঠেছে আজকের দুনিয়ায় পপুলিস্ট লিডারদের উত্থানের প্রধান হাতিয়ার; সেখানে বাংলাদেশের মতো বেশ কিছু রাষ্ট্রে নির্বাচনী ব্যবস্থাই প্রায় তিরোহিত হওয়ার পর্যায়ে। অথচ এসব রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালীতে পপুলিজম বলে কথিত সমস্ত প্রবণতাই হাজির। এই ফেনোমেননকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
পার্থ চট্টোপাধ্যায়: একটা কথা আমি আগে বলেছিলাম। পপুলিজমের জন্য একটা নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কারণ পপুলিস্ট নেতা বা নেত্রী যিনিই থাকুন, বা পপুলিস্ট দল, তাকে সবসময় এইটা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় যে, আমি বৈধভাবে ক্ষমতায় আছি তার কারণ আমি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। এইটা তাকে ক্রমাগত কিছু দিন পরপরই প্রমাণ করতে হয়৷ কিন্তু এই নির্বাচন ব্যবস্থা প্রায় সময়ই অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থা হয় না যদিও একটা বা একাধিক বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নেয়। এটাই একটা অদ্ভুত ঘটনা। আমাদের ভারতবর্ষেও অনেক সময় শুনি যে, বিরোধী শূন্য রাজনীতি হবে। এখন বিরোধী শূন্য নির্বাচনী গণতন্ত্র তো হতে পারে না। এটা কিন্তু সেই অর্থে ডিক্টেটরশিপও থাকছে না। কারণ কোথাও এই প্রয়োজনটা স্বীকার করা হচ্ছে যে, একটা সংবিধান থাকবে, সেই সংবিধানে একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে৷ অথচ সেই নির্বাচনে আমি সকলকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেব না। এমন কিছু লোককেই দাঁড়াতে দেবো যাদের আমি খুব সহজেই পরাস্ত করতে পারি। ফলে আমি যে নির্বাচন করলাম, এবং আমি যে কিছু বিরোধীকে হারিয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে জিতে ক্ষমতায় রইলাম, এই মতটা প্রতিষ্ঠা পায়। এইখানে আপনি যেটা বলছেন যে, এক অর্থে এটা গণতন্ত্রের পারভারশন হয়ে যাচ্ছে। একটা অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের খোলসটা ছাড়া প্রায় আর কিছুই থাকছে না। আমি এইটুকুই বলবো যে, এটা জনবাদের প্রায় শেষ অবস্থা, যেখানে শুধু খোলসটা থাকছে। কিন্তু খোলসটা রাখার প্রয়োজনটাও থাকছে। একটা গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে উঠে এসেছি, এই ধারণাটা তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে খোলসটা রেখে। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম, বার্মায় যে সেনারা ক্ষমতা নিয়েছে, তারাও কিন্তু বলছে যে, আমরা কদিন বাদেই আবার একটা নির্বাচন করব। এবং জানি না, বলা যায় না, হয়তো তারা সেটা করবেও। সেটা তাদের পরিচালনায় অত্যন্ত কুৎসিত কিছু একটা হবে। কিন্তু জনবাদী রাজনীতি নিয়ে আপনি অন্য যে প্রশ্নটা করলেন, জনবাদী রাজনীতি কি কোথাও গিয়ে জনবাদের মূলশর্ত ছাড়িয়ে অন্য কিছু হয়ে যাচ্ছে কিনা? এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ যেখানে বিরোধী দলকে, বিশেষ করে যারা প্রধান বিরোধী দল হতে পারে, তাদের নির্বাচনে অংশই নিতে দেওয়া হচ্ছে না, অথচ একটা নির্বাচন করা হচ্ছে, সেটা কি আদৌ নির্বাচনী গণতন্ত্রের মধ্যে থাকছে? আমার মনে হয়, তা সত্ত্বেও যে প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে যে, তা হলো যে নির্বাচনটা করতে হচ্ছে কেন? আমি যে নির্বাচিত নেতা বা নেত্রী, সেটা প্রমাণ করা এত জরুরি কেন?
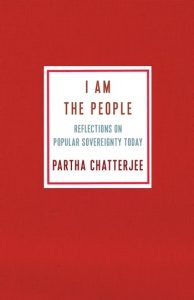
প্রশ্ন ৬: আপনার I Am The People: Reflections On Popular Sovereignty Today বইতে আপনি উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিমে পপুলিজমের উত্থান ঘটেছে tactical contraction-এর মাধ্যমে। আর ইন্ডিয়ায় পপুলিজমের উত্থান ঘটেছে tactical extension-এর মাধ্যমে। এই বিষয়টি আরেকটু ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করছি।
পার্থ চট্টোপাধ্যায়: পশ্চিম প্রসঙ্গে আমি ট্যাক্টিকাল সংকোচনের কথা খানিকটা বলেছিলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে এই: ওয়েলফেয়ার স্টেট থেকে যখন নিও–লিবারাল প্রশাসনের দিকে চলে গেল, তখন সমগ্র জনগণের জন্য কল্যাণমূলক যেসব প্রকল্প ওয়েলফেয়ার স্টেটে নেওয়া হয়েছিলো, সেখান থেকে ক্রমশ সরকারের কল্যাণমূলক কাজে অংশ নেওয়াটা কমে আসতে লাগলো। এটা ‘ট্যাক্টিকাল কন্ট্রাকশন’। এই সংকোচন থেকেই কিন্তু পরবর্তী কালের বাজারনির্ভর আর্থিক অসাম্যের দিকটা, ইনইকুয়ালিটি, প্রকট হয়ে উঠল, যার থেকে পাশ্চাত্যের পপুলিজম, সেটা দক্ষিণপন্থীই বলুন, আর বামপন্থীই বলুন, দুই–ই কিন্তু ওই অসাম্যের ধারণা থেকে আসছে। এই অসাম্য তৈরি হয়েছে ওই কন্ট্রাকশনের পরবর্তীকালে।
অন্যদিকে এশিয়া–আফ্রিকার দেশে কিন্তু জনকল্যাণমূলক ওয়েলফেয়ার স্টেট কোথাওই ছিলো না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্র এখানে পশ্চিমের মতো করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি৷ এইখানে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলোনিয়াল অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রয়োজনে। কলোনিয়াল রাষ্ট্র আসলে খুব অল্প কিছু মানুষের অংশ নিয়ে তৈরি হয়েছিলো। আপনি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কথা যদি ভাবেন, সেখানে ব্রিটিশ শাসক ছিলো, ব্রিটিশ শাসকদের আশেপাশে কিছু ভারতীয় ছিলো, সেই ভারতীয়রা বিভিন্ন রকমের প্রশাসনিক এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই শাসনব্যবস্থায় অংশ নিতে শুরু করে। তারপরে যখন ব্রিটিশ চলে যায়, তখন ভারতবর্ষ আজকের ইন্ডিয়া, পাকিস্তান হলো, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হলো। সেখানে যে শাসন ব্যবস্থা, সেটা ওই কলোনিয়াল শাসন ব্যবস্থাকেই অবলম্বন করে একেকটা জাতীয় রাষ্ট্রের চেহারা নিয়েছে। কিন্তু কোনো সময়েই এখানে আপামর মানুষের মধ্যে প্রায় নাগরিক অধিকারের মতো করে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া, এটা এইসব দেশে কোনো সময়েই ছিলো না।
সুতরাং এসব অঞ্চলে পপুলিজমটা এসছে আসলে একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যে রাষ্ট্র, তার থেকে আস্তে–আস্তে প্রশাসনের কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে। প্রশাসন আসলে ট্যাক্টিকালি এক–একটি জনগোষ্ঠীর দিকে আস্তে–আস্তে এগোবার চেষ্টা করেছে। আপনি যদি ভাবেন, একসময় সরকারি ব্যবস্থা বলতে শুধু একেকটা জেলার সদরে সরকারের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যেত। গ্রামাঞ্চলে গেলে সরকার বলে কিছু দেখতেই পাওয়া যেতো না। গ্রামাঞ্চলে সরকার বলতে ছিলো একটা থানা, একটা বড় জেলার মধ্যে হয়তো ৫টা, ৬টা থানা। এর বাইরে ব্যাপক গ্রামাঞ্চল, সেখানে সরকারি কোনো কর্মচারির কোনো উপস্থিতিই ছিলো না। ধীরে ধীরে এটা বাড়তে শুরু করে। এই যে বাড়া, আস্তে আস্তে একটা করে হেলথ সেন্টার তৈরি হলো, একটা করে সরকারি স্কুল তৈরি হলো, পরবর্তীকালে নানা রকম স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন রকমের সরকারি অফিস। এখন যেমন ধরুন, একটা বাচ্চা জন্মালেই তার একটা সার্টিফিকেট নেওয়া যায়। এটা এখন গ্রামাঞ্চলেও চালু হয়েছে। একসময় তো শহরেও এর ব্যবস্থা ছিলো না। আমার তো কোনো বার্থ সার্টিফিকেট নেই। আমি যখন জন্মেছিলাম, তখন এর কোনো প্রচলনই ছিলো না। আস্তে–আস্তে ধীরে–ধীরে দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রবেশ ঘটেছে। ধরুন, একটা রেশন ব্যবস্থা তৈরি হলো। সরকারি রেশনের দোকান থেকে খানিকটা অল্প মূল্যে খাদ্য পাওয়া যায়। বা অন্যান্য সরকারি যে প্রকল্প, এগুলো ধীরে ধীরে এক্সটেন্ডেড হয়েছে। এই এক্সটেনশনের মাধ্যমে একটা ব্যাপক জনবাদী রাজনীতির জন্ম হয়েছে। সুতরাং এই তফাৎটা আমি করার চেষ্টা করেছি যে পাশ্চাত্যে যে পরিস্থিতির মধ্যে জনবাদী রাজনীতি আজকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ বা এশিয়া আফ্রিকার অন্যান্য দেশে জনবাদী রাজনীতির সামাজিক ভিত্তিটা কিন্তু অন্যরকম।




